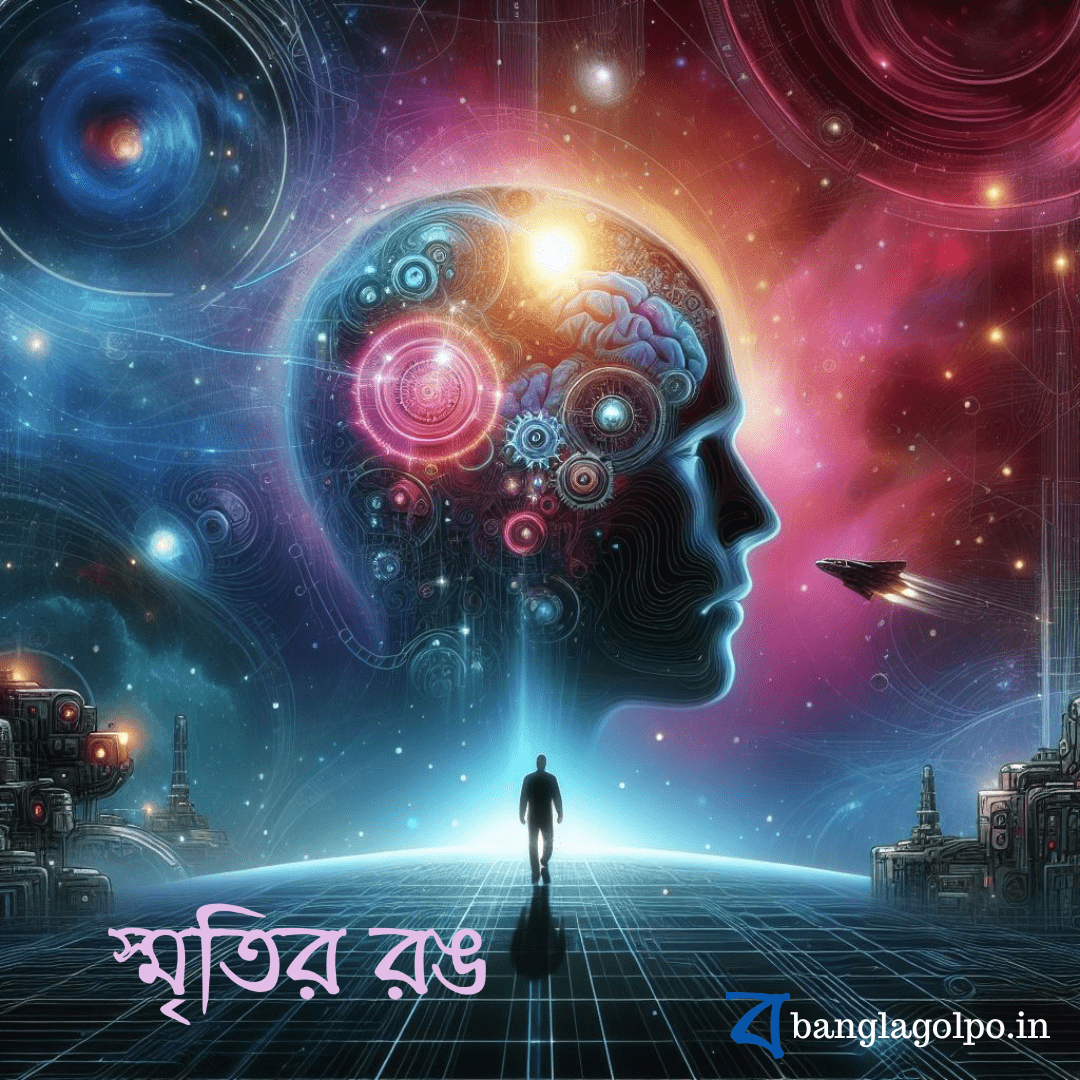কলকাতার বাতাসে এক অদ্ভুত স্বর কাঁপছিল সেদিন। বৃষ্টি নামছিল না, তবুও একটা মৃদু, স্যাঁতসে গন্ধ ছিল বাতাসে। আমি, অহনা, আমার ছাদে দাঁড়িয়ে ছিলাম, চোখ বন্ধ করে সেই গন্ধ টানছিলাম বুকে। সেই গন্ধ – মাটির, আকাশের, আর একটু বাতাসির আবিরের মিশ্রণ। এই গন্ধটা ঠাকুরদাকে মনে করিয়ে দিত।
ঠাকুরদা, আমার শিল্পের গুরু, আমার অনুপ্রেরণা, আমার সবচেয়ে বড় সমালোচক। তিনিই ছিলেন সেই মানুষ, যিনি প্রথম আমার ছবিতে প্রতিভা দেখেছিলেন, আমার হাত ধরে রঙের জগতে নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু দু’বছর আগে, ঠাকুরদা চলে গেছেন। আর তার সঙ্গে চলে গেছে আমার শিল্পের প্রাণ।
ঠাকুরদা চলে যাওয়ার পর থেকে আমার আর ছবি আঁকা হয় না। আগে আমার ছাত ছিল রঙের খেলায়, ক্যানভাসে ঝরে পড়তো আনন্দ-বিষাদ, আশা-হতাশার নানান রঙ। কিন্তু এখন আমার প্যালেটে শুধুই একটা রঙ – শূন্যতার ধূসর। আমি চেষ্টা করেছি, সত্যিই চেষ্টা করেছি আঁকারের তাগ ডোমাতে। কিন্তু প্রতিবারই মাথায় জ্বালা শুরু হয়ে যায়, যেন কেউ ভিতর থেকে আমার মস্তিষ্ক খুঁড়িয়ে দিচ্ছে।
এই শূন্যতা, এই অসহ্য মাথাব্যথা নিয়ে দিন কাটছিলাম। একদিন, পুরনো খাতা ঘাটতে গিয়ে জনা চক্রবর্তীর একটি লেখা চোখে পড়ল। জনা চক্রবর্তী – এক বিখ্যাত নিউরোসাইন্টিস্ট, যিনি মস্তিষ্কের গোপন কামরায় ঢুঁ মারার চেষ্টা করছিলেন। লেখাটিতে তিনি একটা নতুন আবিষ্কারের কথা লিখছিলেন – মৃত মানুষের স্মৃতি ডিজিটাল উপায়ে সংরক্ষণের সম্ভাবনা।
এই লেখা পড়ে আমার মনে একটা আশার আলো জ্বলে উঠল। যদি ঠাকুরদার স্মৃতিগুলোকে ডিজিটালি সংরক্ষণ করা যায়, তাহলে হয়তো আমার হারানো অনুপ্রেরণা ফিরে পাব। জনা চক্রবর্তীর ল্যাবের ঠিকানা খুঁজে বার করতে আমার বেশি সময় লাগল না। পরের দিনই আমি তাঁর ল্যাবে গিয়ে হাজির।
জনা চক্রবর্তী ছিলেন মৃদুভাষী, বয়স্ক একটা মানুষ। তিনি আমার গল্প শুনলেন, তারপর চিন্তা করে বললেন, “আপনার ঠাকুরদার কোনো ব্যক্তিগত জিনিস আছে?” আমি তাকে ঠাকুরদার পুরনো ব্রাশ, রঙের টিউব এবং ব্যবহার করা প্যালেট দেখালাম। জনা সেগুলো নিয়ে তাঁর ল্যাবের একটা যন্ত্রের সঙ্গে সংযুক্ত করলেন। যন্ত্রটি একটা বিশাল কম্পিউটারের মনিটরে হঠাৎ রঙের ঝলক দেখা দিল। জনা চক্রবর্তী কিছু কিছু বোতাম চেপে দিলেন, তারপর আমার দিকে চোখ রেখে বললেন, “আপনি দেখুন, অহনা।”
মনিটারে এলোমেলো রঙের আঁচড় দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই আঁচড়গুলো আস্তে আস্তে স্বচ্ছ হয়ে উঠল। পর্দায় ফুটে উঠল একটা আলোর টান। ঢেউ খেলানো সবুজের মাঠ, তার উপর একটা বিশাল গাছের ছায়া। ঠাকুরদার ছবি আঁকার স্টাইল, ঠিক যেমনটা তিনি আঁকতেন।
আমি অবাক হয়ে গেছিলাম। ঠাকুরদার স্মৃতি, তাঁর শিল্পী মন, সব কিছুই যেন এই ডিজিটাল রঙের মাধ্যমে ফিরে এসেছে। জনা চক্রবর্তী আমার অবাক চাহনি দেখে হাসলেন, “এই প্রযুক্তি এখনো অনেকটা অসম্পূর্ণ অবস্থায় আছে। কিন্তু আপনার ঠাকুরদার স্মৃতির কিছু অংশ আমরা এভাবে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছি।”
আমার চোখে জল এসে গেল। ঠাকুরদার স্মৃতির এইটুকু আমার জন্যে যথেষ্ট ছিল। পরের কয়েকদিন ধরে আমি প্রতিদিন জনা চক্রবর্তীর ল্যাবে যেতাম। তিনি আমাকে ঠাকুরদার স্মৃতির আরো কিছু অংশ দেখালেন – ছেলেবেলায় ঠাকুরদা যে ফুলের ছবি আঁকতেন, সেই ছবির কিছু অংশ, ঠাকুরদা রঙের মিশ্রণ নিয়ে পরীক্ষা করার কিছু মুহূর্ত। এই স্মৃতির টুকরোগুলো আমাকে যেন ঠাকুরদার সঙ্গে নিয়ে ফিরিয়ে দিয়েছে।
একদিন, ল্যাবে যাওয়ার সময় আমার সাথে ঠাকুরদার পুরনো রঙের বাক্সটাও নিয়ে গেলাম। সেই বাক্সটা খুলে জনা চক্রবর্তী অবাক হয়ে গেলেন। বাক্সের একটা গোপন কুঠুরি ছিল, সেখানে ঠাকুরদার ব্যবহার করা একটা বিশেষ ধরণের ব্রাশ ছিল। জনা সেই ব্রাશটা যন্ত্রের সঙ্গে সংযুক্ত করলেন। মনিটারে আবার রঙের ঝলক দেখা দিল।
কিন্তু এবারের ছবিটা আগের সব ছবির থেকে আলাদা ছিল। এটা কোনো ল্যান্ডস্কেপ বা পোরট্রেট ছিল না। ছবিতে ছিল একটা বিশাল গোলক, যার ভিতরে অসংখ্য রঙের রেখা ঘুরে চলছিল। ঠাকুরদা কি এটা আঁকতে চেয়েছিলেন? এই অসম্পূর্ণ ছবিটা আমার মনে এক অদ্ভুত প্রশ্ন জাগিয়ে দিল।
ঠাকুরদা কি আমার কাছ থেকে কিছু লুকিয়ে রাখছিলেন? এই রহস্যের উত্তর খুঁজতে আমি জনা চক্রবর্তীর সাহায্য নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম।
জনা চক্রবর্তী মনিটারের দিকে চেয়ে চিন্তাভাবনা করলেন। “এটা খুবই আকর্ষণীয়,” তিনি বললেন, “এই ছবিটা ঠাকুরদার মনের কোন গভীরতর চিন্তার প্রতিফলন হতে পারে। কিন্তু আমার মেশিন এখনো এতটা উন্নত নয় যে, আমরা এই ছবির অর্থ সঠিকভাবে বুঝতে পারি।”
আমার মনে একটা জেদ জাগল। ঠাকুরদা যে এই ছবি আঁকতে চেয়েছিলেন, সেটা স্পষ্ট। কিন্তু কেন? এই অসম্পূর্ণ ছবির পেছনে কি রহস্য লুকিয়ে আছে? আমি জনা চক্রবর্তীকে জানালাম, “আমাকে এই ছবির অর্থ খুঁজে বের করতে হবে। ঠাকুরদা আমার কাছ থেকে কিছু লুকিয়ে রেখেছিলেন, এই ছবিটাই তার প্রমাণ।”
জনা চক্রবর্তী আমার কথা ভাবলেন, তারপর বললেন, “ঠিক আছে, আমরা চেষ্টা করে দেখতে পারি। কিন্তু এটা খুব কঠিন কাজ হতে পারে। ঠাকুরদার আরো বেশি স্মৃতি আমাদের উদ্ধার করতে হবে, এমন কিছু স্মৃতি, যেগুলো হয়তো এই ছবির সাথে সম্পর্কিত।”
আমি জনা চক্রবর্তীর কথায় সম্মতি জানালাম। পরের কয়েক সপ্তাহ ধরে আমরা দু’জনে মিলে কাজ করলাম। ঠাকুরদার পুরনো নোটবই, চিঠিপত্র, এমনকী তাঁর স্টুডিওর দেওয়ালে ঝুল জড়ানো খোলখাটা সব কিছুই আমরা ঘাঁটলাম। এই সব কিছুর মধ্যে কিছু সূত্র পেলাম। ঠাকুরদা কয়েক বছর ধরে একটা বিশেষ ধরণের শিল্প নিয়ে গবেষণা করছিলেন। সেই শিল্পের কথা তিনি কাউকে বলেননি, এমনকি আমাকেও না।
এই গবেষণার নোটগুলি পড়ে বুঝলাম, ঠাকুরদা এমন একটা শিল্প ধারা আবিষ্কারের চেষ্টা করছিলেন, যেখানে শিল্পী তাঁর নিজের মস্তিষ্কের গতিবিধি, স্মৃতি আর চারণাকেই ক্যানভাসে ফুটিয়ে তুলবেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, এই শিল্পের মাধ্যমে মানুষের মনের গভীরতা আবিষ্কার করা যাবে।
এই তথ্য আমাকে আরো রহস্যের জালে জড়িয়ে দিল। ঠাকুরদা কি এই অসম্পূর্ণ ছবির মাধ্যমে তাঁর নিজের মনেরই একটা চিত্র আঁকতে চেয়েছিলেন? কিন্তু কেন থেমে গেলেন? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে আমি জনা চক্রবর্তীর ল্যাবে আরো ঘনঘন যেতে লাগলাম।
একদিন, ঠাকুরদার একটা চিঠির মধ্যে একটা খাম খুঁজে পেলাম। খামের উপর লেখা ছিল, “অহনার জন্যে”। আমার হাত কাঁপছিল, খামটা খুলে পড়তে শুরু করলাম। চিঠিতে ঠাকুরদা লিখেছিলেন, তিনি একটা নতুন ধরণের শিল্প আবিষ্কার করেছেন, কিন্তু এই শিল্পের কিছু ঝুঁকি আছে।
চিঠিটা পড়তে পড়তে আমার হাত-পা কাঁপছিল। ঠাকুরদা লিখেছিলেন, এই নতুন শিল্পধারায় শিল্পী নিজের মস্তিষ্কের গভীর স্তরে নেমে যান, স্মৃতি ও চারণায় সীমানা অতিক্রম করেন। কিন্তু এই গভীরতা থেকে ফিরে আসা কখনো কখনো কঠিন হয়ে পড়ে। কিছু ক্ষেত্রে, শিল্পী সেই গভীর স্তরেই আটকে যেতে পারেন, মনের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলতে পারেন।
ঠাকুরদা জানতেন এই পথের ঝুঁকি। তবুও তিনি এই নতুন শিল্পধারা আবিষ্কারের চেষ্টা করেছিলেন। আর সেই চেষ্টারই ফল হয়তো এই অসম্পূর্ণ ছবি।
ঠাকুরদার চিঠি পড়ে আমার বুকটা এমন জ্বালা করে উঠল, যেন কেউ একটা পাথর চাপিয়ে দিয়েছে। ঠাকুরদা আমার কাছে এসব কিছু লুকিয়ে রাখলেন কেন? তিনি কি এই ঝুঁকির কথা জানতেন না? না জেনেই কি এই পথে পা দিয়েছিলেন?
জনা চক্রবর্তীকে চিঠিটা দেখালাম। তিনি চিঠি পড়ে চুপ করে কিছুক্ষণ বসে রইলেন। তারপর বললেন, “অহনা, এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। ঠাকুরদা নিজের মনের একটা গভীর স্তরে নেমে গিয়েছিলেন, আর সেখান থেকে বের হতে পারেননি। হয়তো এই অসম্পূর্ণ ছবিই তার সেই অবস্থার একটা প্রতিফলন।”
আমার চোখে জল এসে গেল। ঠাকুরদা শিল্পের প্রতি এতটা নিবেদিত ছিলেন যে, নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়েও এই নতুন ধারা আবিষ্কারের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সেই চেষ্টাই তাঁকে চিরতরে নিঃশব্দ করে দিয়েছিল।
কিন্তু এখনো একটা প্রশ্ন আমার মনে থেকে গেল। ঠাকুরদা যদি নিজের মনের গভীরে আটকে গিয়ে থাকেন, তাহলে কি তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব? জনা চক্রবর্তীকে এই প্রশ্ন করলাম।
জনা চক্রবর্তী মাথা নাড়লেন। “আমার টেকনোলজি এখনো এতটা উন্নত হয়নি। তবে হয়তো ভবিষ্যতে…”। কথাটা শেষ না করেই তিনি থামলেন।
আমি জানতাম, এখনই ঠাকুরদার সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব নয়। তবে ঠাকুরদার শেষ চেষ্টার ফসল, এই অসম্পূর্ণ ছবিটাকেই আমি শেষ করব। ঠাকুরদা যে পথে পা দিয়েছিলেন, সেই পথেই হাঁটব, তাঁর গবেষণাকে আরো এগিয়ে নেব। হয়তো একদিন আমিই ঠাকুরদার সেই শিল্পধারা আবিষ্কার করতে পারব, আর সেই সাথে ঠাকুরদার সঙ্গেও যোগাযোগ স্থাপন করতে পারব।
এই লক্ষ্যে আমি জনা চক্রবর্তীর সাহায্য নিয়ে কাজ শুরু করলাম। ঠাকুরদার ছেড়ে ফেলা পথটা আমি আরো একবার চললাম। সপ্তাহের পর সপ্তাহ কেটে গেল। ল্যাবে আমি আর জনা চক্রবর্তী দু’জনে মিলে নিরলস কাজ করলাম। ঠাকুরদার ছেড়ে ফেলা পথটা পূরণ করার চেষ্টা চললো পুরোদমে।
ঠাকুরদার গবেষণা নোটের সূত্র ধরে আমরা একটা যন্ত্র তৈরি করলাম। এই যন্ত্রের সাহায্যে নিজের মস্তিষ্কের গতিবিধি ক্যানভাসে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হবে। ঈশ্বর জানে, কাজটা ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। তবে ঠাকুরদার ছেড়ে ফেলা চেষ্টাটা শেষ করার এবং তাঁর সঙ্গে যোগাযোগের আশায় আমি এই ঝুঁকি নিতে রাজি ছিলাম।
শেষ পর্যন্ত যন্ত্রটা তৈরি হলো। জনা চক্রবর্তী আমাকে সাবধানে থাকতে বললেন। আমি মাথা কুঁ দিয়ে যন্ত্রের সাথে যুক্ত হলাম। চোখ বন্ধ করে নিঃশ্বাস নিলাম। যন্ত্রটা চালু হলো।
প্রথমে কিছুই বুঝতে পারলাম না। তারপর ধীরে ধীরে রঙের ঝিলিক দেখতে লাগলাম। নীল, সবুজ, লাল – রঙের এক অদ্ভুত মিশ্রণ। এই রঙের ঝিলিকের ভেতরে কখনো একটা মুখের আভা দেখা দিল, কখনো বা একটা বিশাল গাছের ছায়া। ঠাকুরদার স্মৃতির টুকরো টুকরো অংশগুলো আমার চোখের সামনে ভাসছিল।
এর মধ্যেই মাথায় একটা তীব্র জ্বালা অনুভব করলাম। যেন কেউ একটা গরম সূঁচ আমার মস্তিষ্কে গেঁথে দিয়েছে। সহ্য করা যাচ্ছিল না। আর পারছিলাম না। চিৎকার করে উঠলাম, “বন্ধ করুন! বন্ধ করুন!”
জনা চক্রবর্তী তড়িঘড়ি যন্ত্রটা বন্ধ করে দিলেন। আমি যন্ত্রের সাথে থেকে আলাদা হলাম। মাথাটা চড়াচড় করছে। কিন্তু মনে হলো, যেন একটা নতুন দৃষ্টিভঙ্গি আমার মধ্যে জেগে উঠেছে।
পরের কয়েকদিন ঠাকুরদার ছবির দিকে তাকিয়ে থাকলাম। অসম্পূর্ণ গোলকটা এখন আমার কাছে আর অদ্ভুত লাগছিল না। বরং মনে হচ্ছিল, এই গোলকের ভেতরেই রয়েছে আমার ঠাকুরদার আটকে থাকা চলবেনা।
ঠাকুরদার গবেষণা নোট এবং আমার নিজের অভিজ্ঞতা নিয়ে নতুন করে যন্ত্রটা তৈরি করলাম। এবারের যন্ত্রটা আরো উন্নত ছিল। এটা শুধু শিল্পীর মনের গতিবিধিই না, বরং আরেকজনের মনের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতেও সক্ষম হবে।
যন্ত্রটা চালু করলাম। এবার মাথায় কোনো ব্যথা অনুভব করলাম না। গোলকের ভেতরে রঙের খেলা শুরু হলো। ধীরে ধীরে সেই রঙের খেলা থেকে একটা মুখের আকৃতি ফুটে উঠল। ঠাকুরদার মুখ।
চোখ বন্ধ করে, “ঠাকুরদা,” ফিসফিস করে ডাকলাম। একটা দীর্ঘশ্বাসের মতো শব্দ ভেসে এলো যন্ত্রের ভিতর থেকে। তারপর ঠাকুরদার কণ্ঠ – ক্লান্ত, কিন্তু আশার সুরে মেশানো, “অহনা?”
“হ্যাঁ, ঠাকুরদা, এটা আমি, অহনা।” আমার গলা কাঁপছিল।
“অহনা? কিন্তু… কীভাবে?” ঠাকুরদার কণ্ঠে বিস্ময়ের ছাপ।
আমি তাকে সব খুঁটিনাটি জানালাম – জনা চক্রবর্তীর গবেষণা, তার মেশিন, আমার চেষ্টা। ঠাকুরদা সব শুনে কিছুক্ষণ চুপ থাকলেন। তারপর বললেন, “অহনা, আমি বোধহয় একটা ভুল করেছিলাম। এই নতুন শিল্পধারাটা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। আমি নিজের মনের গভীরে নেমে গিয়ে আর ফিরতে পারিনি।”
“কিন্তু ঠাকুরদা, আমি আপনাকে ফিরিয়ে আনব।” আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বললাম।
“না, অহনা।” ঠাকুরদা উত্তর দিলেন, “এই শরীরটা আর আমার নয়। আমি এখন শুধু মাত্র রঙের খেলা, স্মৃতির টুকরো।”
একটা অসহ্য বেদনা আমার বুকে জ্বালা করে উঠল। ঠাকুরদাকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়, এটা বুঝতে পারছিলাম। কিন্তু তবুও তাঁর সঙ্গে এই যোগাযোগ, এই কথাবার্তা – এটাই যেন আমার নতুন সান্ত্বনা হয়ে দাঁড়াল।
ঠাকুরদার সঙ্গে কথা বলতে বলতে দিন কেটে গেল। আমরা শিল্প, জীবন, সব কিছু নিয়ে কথা বলতাম। ঠাকুরদা আমাকে তাঁর অসম্পূর্ণ শিল্পধারা সম্পর্কে আরো কিছু জানালেন।
একদিন ঠাকুরদা বললেন, “অহনা, তুমিই এই শিল্পধারাটা শেষ করো। তুমিই দেখিয়ে দাও, মানুষের মনের গভীরতা ক্যানভাসে ফুটে উঠতে পারে।”
আমি জানতাম এটা খুবই কঠিন কাজ। কিন্তু ঠাকুরদার শেষ ইচ্ছাপূরণ করার জন্যে আমি প্রতিজ্ঞা করলাম।
ঠাকুরদার সাহায্য নিয়ে নতুন করে যন্ত্রটা আরো উন্নত করলাম। এবার এই যন্ত্রের সাহায্যে নিজের মনের গভীরতা ক্যানভাসে ফুটিয়ে তুলতে পারব।
কয়েক মাসের ক্লান্তিহীন পরিশ্রম এর পরে আমি প্রস্তুত হলাম। যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত হলাম, চোখ বন্ধ করে নিঃশ্বাস নিলাম। যন্ত্রটা চালু হলো।
রঙের ঝিলিক, স্মৃতির টুকরো, অনুভূতির ঢেউ – সব কিছু মিশে গেল একাকার। আমি আমার শিল্পের মধ্যে হারিয়ে গেলাম। কখন যে সময় চলে গেল, বুঝতে পারলাম না।
যখন চোখ খুলে তাকালাম, তখন আমার সামনে রয়েছে একটা অসাধারণ ছবি। ঠাকুরদার
ঠাকুরদার অসম্পূর্ণ গোলকের ছবিটা এখন আর অসম্পূর্ণ ছিল না। এটা এখন একটা জটিল জালের মতো ছিল, রঙের স্তরের পর স্তর একে অপরের মধ্যে মিশে গিয়েছিল। কিন্তু এই জটিলতার মধ্যেও একটা স্বচ্ছতা ছিল, একটা গভীরতা, যা আগে কোনো শিল্পে দেখিনি।
আমি জানতাম, এই ছবিটা শুধু রং নয়, এটা আমার এবং ঠাকুরদার মনের মিলন, দুই প্রজন্মের শিল্পীর সহযোগিতা। এটা মানব মনের গভীরতার একটা প্রতিচ্ছবি, স্মৃতির টুকরো আর চেতনার এক অদ্ভুত মিশ্রণ।
এই ছবিটা নিয়ে একটা প্রদর্শনীর আয়োজন করলাম। শিল্প জগতের মানুষজন অবাক হয়ে গেলেন। এমন একটা শিল্পধারা কেউ কখনো দেখেননি। অনেকে প্রশ্ন করলেন, এই ছবি কীভাবে আঁকা হয়েছে। কিন্তু আমি সব কিছু গোপন রাখলাম। ঠাকুরদার ইচ্ছাপূরণই ছিল আমার কাছে সবচেয়ে বড়ো কথা।
এই প্রদর্শনীর পরে আমি আরো অনেক ছবি আঁকলাম, এই নতুন শিল্পধারা ব্যবহার করে। প্রতিটা ছবিই ছিল একটা রহস্য, একটা গল্প, মানব মনের গভীরতার এক অংশ। আমার এই নতুন ধারা শিল্প জগতে ব্যাপক সাড়া ফেলল।
কিন্তু এই সাফল্যের পেছনে সবসময় ঠাকুরদার কথা মনে থাকত। তাঁর সাহস, তাঁর উদ্ভাবনী, আর তাঁর সেই অসম্পূর্ণ ছবি – এসবই ছিল আমার অনুপ্রেরণা। ঠাকুরদা হয়তো শরীরিকভাবে আর আমার সঙ্গে নেই, কিন্তু তিনি ছিলেন, আছেন, এবং থাকবেন আমার শিল্পের মধ্যে, রঙের খেলায়, স্মৃতির টুকরোয়।